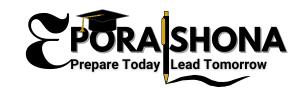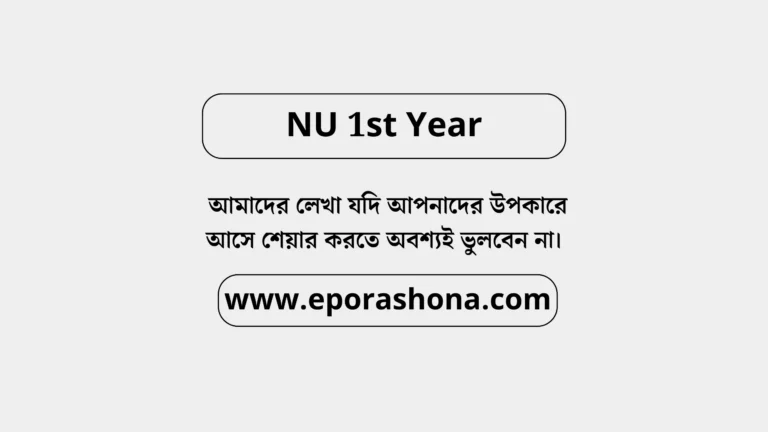পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো। [জা.বি. ২০১৯]★★★
ভূমিকাঃ সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা। শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত নানাবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান কার্যকর কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য সনাতন সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্মের পরিবর্তে আধুনিক পেশাভিত্তিক সমাজকর্মের প্রয়োজন অনুভূত হবার প্রেক্ষিতে এর বিকাশ ঘটে। কেননা পেশা ভিত্তিক হবার কারণে সমাজকর্ম মানুষের বিভিন্ন সংকটে কার্যকরভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে। সমাজকর্ম পেশাগত মর্যাদা চূড়ান্তভাবে অর্জন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে। এ সময়ে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপক অনুশীলন হয়েছে, উদ্ভাবন হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের কৌশল, সর্বোপরি সমাজকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা অর্জন করার সুযোগ পেয়েছে।
পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
সমাজকর্ম একটি পেশাদার কার্যক্রম যা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। পেশাদার সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সমাজের প্রান্তিক এবং অসহায় মানুষদের উন্নয়নে সহায়তা করা এবং তাদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
সমাজকর্মের প্রাথমিক ধারণাঃ সমাজকর্মের ইতিহাস বহু প্রাচীন। সমাজের দুর্বল ও অসহায় সদস্যদের প্রতি সাহায্য এবং সহানুভূতির ধারণা বিভিন্ন সভ্যতার প্রাচীন রীতিনীতিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সভ্যতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজসেবার দায়িত্ব পালন করত। ভারতীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমান সভ্যতায় দাতব্য কাজ এবং সামাজিক সাহায্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অসহায়দের সাহায্য করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা সমাজকর্মের ভিত্তি স্থাপন করে।
পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব
১. মধ্যযুগে সমাজসেবাঃ মধ্যযুগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন, চার্চ) দারিদ্র্যপীড়িত এবং অসুস্থ মানুষদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করত। তবে এই সময় সমাজসেবা ছিল স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত। সমাজকর্ম তখনো একটি পেশা হিসেবে বিকশিত হয়নি।
২. পুনর্জাগরণ এবং দাতব্য আইনঃ ১৫৪৭ সালে ইংল্যান্ডে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্র সমাজের দরিদ্র জনগণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৬০১ সালের “ইংলিশ পুওর ল” (English Poor Law) সমাজকর্মের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আইনের মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। এটি পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে।
৩. শিল্পবিপ্লব এবং নগরায়নঃ ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলে নগরায়ন এবং আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটে। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের অভিবাসনের ফলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, এবং অপরাধ বৃদ্ধি পায়। শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। এই সময় দাতব্য সংস্থা এবং ফাউন্ডেশনগুলো সমাজসেবার জন্য এগিয়ে আসে।
৪. সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপঃ সমাজকর্ম ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য দাতব্য সংস্থা এবং সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৮৮৯ সালে লন্ডনের টয়নবি হল এবং ১৮৮৬ সালে শিকাগোতে হাল হাউজ প্রতিষ্ঠা সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথ প্রশস্ত করে।
পেশাদার সমাজকর্মের ক্রমবিকাশ
১. বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষাঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৮ সালে নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মতো সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯২০ সালে কেস ওয়ার্ক (Case Work), গ্রুপ ওয়ার্ক (Group Work), এবং কমিউনিটি সংগঠনের (Community Organization) ধারণাগুলো সমাজকর্ম শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।
২. আন্তর্জাতিক সমাজকর্মের বিকাশঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতিসংঘের মাধ্যমে সমাজকর্ম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন, শরণার্থীদের সহায়তা, এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মতো কার্যক্রম সমাজকর্মকে বৈশ্বিক মাত্রা দেয়। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক সমাজকর্ম সংগঠন (International Federation of Social Workers) প্রতিষ্ঠা করা হয়।
৩. গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে সমাজকর্মঃ সমাজকর্ম একটি পেশা হিসেবে উন্নত হওয়ার জন্য গবেষণা ও নীতিনির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০শ শতাব্দীতে সমাজকর্ম গবেষণার ওপর জোর দেওয়া হয়। সমাজের সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করে।
বাংলাদেশে সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ
বাংলাদেশে সমাজকর্মের বিকাশে উপমহাদেশীয় ঐতিহ্যের প্রভাব রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে দাতব্য কাজের প্রচলন ছিল ধর্মীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।
১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণঃ ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণ বিভাগ চালু হয়। এটি বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি স্থাপন করে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।
২. সরকারি উদ্যোগঃ বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। গ্রামীণ উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার, এবং দরিদ্রদের জন্য ভাতা প্রদান সমাজকর্মের আওতায় পড়ে।
৩. বেসরকারি সংস্থা (এনজিও): বাংলাদেশে এনজিওগুলো সমাজকর্মের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, এবং আশার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে।
সমাজকর্মের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
১. ডিজিটাল সমাজকর্মঃ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকর্ম আরও কার্যকর করা সম্ভব। ই-গভর্নেন্স, অনলাইন কাউন্সেলিং, এবং সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সমাজসেবার প্রচার ও প্রসার সম্ভব।
২. পরিবেশ সমাজকর্মঃ পরিবেশগত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সমাজকর্মীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুনর্বাসন সমাজকর্মের ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র হতে পারে।
৩. গবেষণা ও উদ্ভাবনঃ সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবিত হতে পারে। বিশেষ করে নারী অধিকার, শিশু সুরক্ষা, এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমাজকর্মের অগ্রাধিকার হতে পারে।
উপসংহারঃ পেশাদার সমাজকর্ম একটি পরিবর্তনশীল পেশা যা মানুষের জীবনমান উন্নত করতে এবং সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে অবদান রাখে। এর উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, এবং সামাজিক পরিবর্তনগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সমাজকর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও এই পেশার গুরুত্ব আরো বাড়বে।